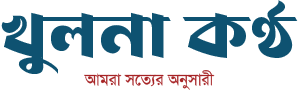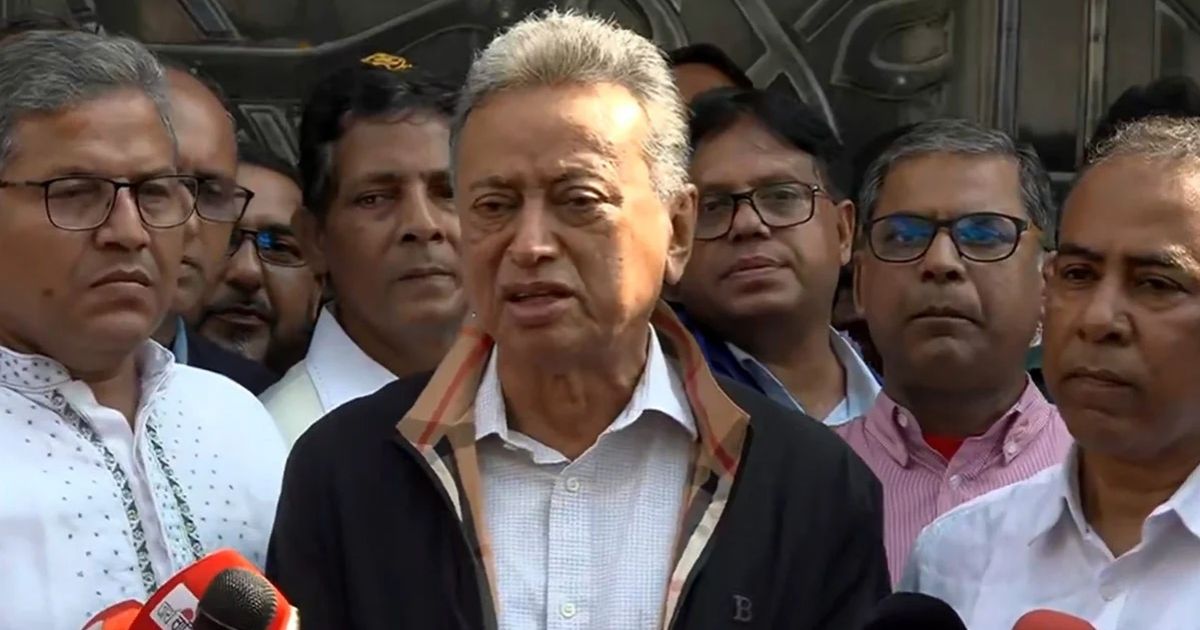২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ লাখ ৮১ হাজার কোটি টাকা বেশি। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ এই পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত ‘ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০২৪’ অনুযায়ী, এক বছরে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের পরিমাণ ৪৪.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইএমএফের সংজ্ঞা অনুসারে, খেলাপি, পুনঃতফসিলকৃত এবং অবলোপনকৃত (রাইট-অফ) ঋণসহ সব মিলিয়ে এই দুর্দশাগ্রস্ত ঋণগুলোকে গণ্য করা হয়।
একই রিপোর্টে বলা হয়, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, পুনঃতফসিলকৃত ঋণ ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা, আর রাইট-অফকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দেওয়া ঋণ এমনভাবে বেড়েছে যে এখন তা খেলাপিতে পরিণত হচ্ছে। আগে এই তথ্যগুলো গোপন থাকলেও, আইএমএর চাপের মুখে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন নিয়মিতভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করছে।
প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, চলতি বছর ব্যাংক খাতের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে মূলধনের নিরাপত্তা বিষয়ে। ক্যাপিটাল টু রিস্ক-ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও (সিআরএআর) শুধু ৩.০৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যেখানে আন্তর্জাতিক মানে এই অনুপাত কমপক্ষে ১০ শতাংশ থাকা উচিত। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কিছু ইসলামী ব্যাংকের।
মূলধন ও লিভারেজ অনুপাত যথাক্রমে ০.৩০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাংকিং খাতে কাঠামোগত দুর্বলতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাবের চিত্র দেখায়।
তবে, ব্যাংকখাতের তরলতা পরিস্থিতি এখনও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে। অ্যাডভান্স-ডিপোজিট রেশিও (এডিআর) ৮১.৫৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক খাত সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও, ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে খেলাপি ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ এবং সুশাসনের অভাব। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী নীতি, কঠোর তদারকি এবং প্রযুক্তিনির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারের সদর্থক পদক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের একযোগে কাজ করা দরকার।